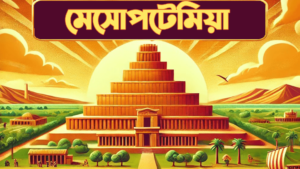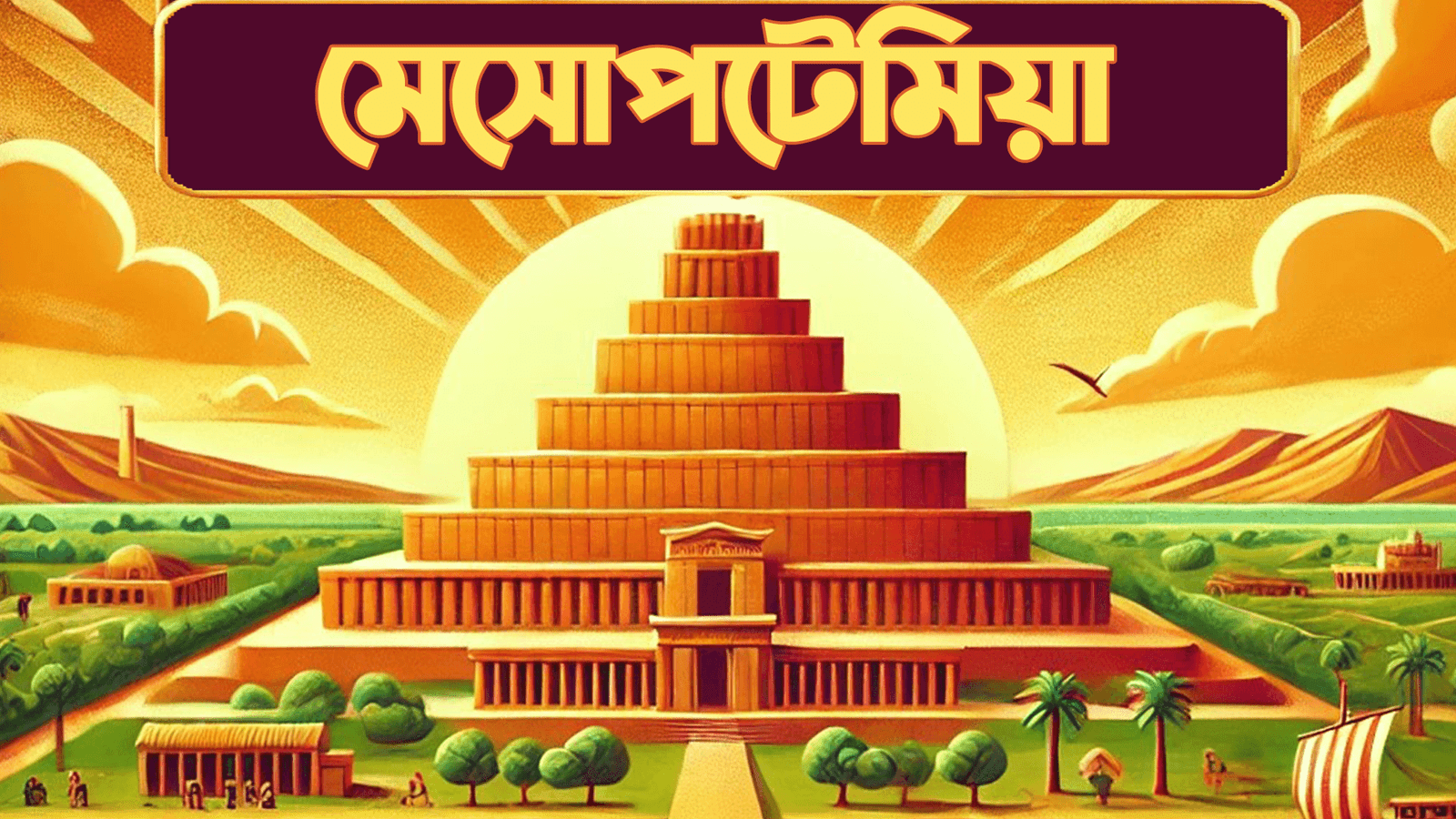ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত সিন্ধু নদকে কেন্দ্র করে খ্রি.পূ. ৩৩০০ থেকে ১৩০০ খ্রি. পূর্বাব্দে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাকেই ইতিহাসে সিন্ধু সভ্যতা নামে ডাকা হয়। ১৯২০-এর দশকে তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে এই সভ্যতার প্রথম শহর হরপ্পা আবিষ্কৃত হয়। তাই সিন্ধু সভ্যতা হরপ্পা সভ্যতা নামেও পরিচিত। উন্নত নগর পরিকল্পনা, বৃহৎ স্নানাগার, পরিমাপনবিদ্যা, ভাস্কর্য ইত্যাদি নিদর্শন প্রমাণ করে যে এই সভ্যতা সেসময়ের তুলনায় অত্যন্ত উন্নত ছিল।
ভারতীয় উপমহাদেশের উন্নত সেই সভ্যতা সম্পর্কে জানাতেই আমাদের আজকের নিবেদন সিন্ধু সভ্যতা।
ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়
সিন্ধু সভ্যতা বর্তমান পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের পশ্চিমদিকের রাজ্যগুলি, দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তান এবং বেলোচিস্তান প্রদেশের পূর্ব অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল।
প্রধান শহরগুলোর মধ্যে
- হরপ্পা পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের সাহিওয়াল জেলায় এবং
- মহেঞ্জোদারো সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় অবস্থিত।
সিন্ধু সভ্যতার মোট আয়তন ১২,৬০,০০০ কি.মি. এবং জনসংখ্যা ৫০ লক্ষেরও বেশি ছিল।
ভারতের মূল নিবাসী দ্রাবিড়দের হাত ধরেই গড়ে উঠেছিল এই সভ্যতা।
এই সভ্যতায় লৌহের ব্যবহার না থাকায় এটি অনুমান করা যায় যে লৌহ যুগের পূর্বেই সভ্যতাটি ধ্বংশ হয়ে যায়। অর্থাৎ এটি ছিল ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা।
সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য
উন্নত নগর ব্যবস্থা
সিন্ধু সভ্যতা প্রাচীন বিশ্বের প্রথম বৃহৎ নগর সভ্যতাগুলোর একটি। প্রধান শহরগুলো তথা হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো ইত্যাদি পরিকল্পিতভাবে নির্মিত ছিল। রাস্তা ও গলিপথগুলো সোজা ও পরস্পরের সঙ্গে সুষম কোণে ছিল। উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থা জল নিষ্কাশনে অত্যন্ত কার্যকর ছিল। ঘরবাড়ি পোড়ামাটির ইট দিয়ে তৈরি ছিল। বাড়ির আকার ও গুণমান ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যেত। বড়, সাজানো ঘরগুলো অভিজাতদের জন্য এবং ছোট ঘর বা কুটির নিম্নশ্রেণির জন্য ব্যবহৃত হতো।
সামাজিক কাঠামো
সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিল। যেমন: শাসক, পুরোহিত, কারিগর, কৃষক ইত্যাদি। পেশা অনুযায়ী সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি ছিল। শাসক ও পুরোহিতরা ছিল সবার উপরে আর কৃষক, শ্রমিক ও দাসরা ছিল সবার নিচের শ্রেণিতে।
সিন্ধু সভ্যতায় নারীরা সন্তান পালন, গৃহস্থালি কাজ এবং বস্ত্র নির্মাণে নিযুক্ত ছিলেন। সমাজে নারীদের মর্যাদাও মোটামুটি ভালো ছিল।
অর্থনীতি
সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা গম, যব, তুলা ইত্যাদি চাষ করত। এছাড়া খেজুর, বদরী, আনারস ও আঙ্গুর উৎপাদন করত। কার্পাসের চাষও ভালো হতো। তারা নদীর পানি ব্যবহার করে সেচব্যবস্থা পরিচালনা করত। কৃষিজ যন্ত্রপাতি যেমন লাঙলের ব্যবহার করত।
গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি পালন করত।
মেসোপটেমিয়া, পারস্য ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা বাণিজ্য করত। বাণিজ্যের প্রধান পণ্য ছিল তুলা, তামা, লোহা, মসলা, শস্য ও সীলমোহর। সীলমোহরগুলোতে পশু, দেবতা ও প্রতীক খোদাই করা থাকত এবং এগুলো বাণিজ্যের প্রমাণ বহন করত।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
সিন্ধু সভ্যতার মানুষ প্রকৌশল, নির্মাণ, জলব্যবস্থাপনা, ওজন ও পরিমাপের মতো ক্ষেত্রে চমৎকার দক্ষতা দেখিয়েছিল।
এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে একক ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থার উদ্ভাবন। তারা ব্রোঞ্জের দাড়িপাল্লা, বিভিন্ন আকৃতির বাটখারা, স্কেল ইত্যাদি ব্যবহার করতো। দৈনন্দিন কাজ ও বাণিজ্যের জন্য তারা এই পরিমাপনবিদ্যা ব্যবহার করত।
তারা কাঠের তৈরি চাকা ও গাড়ি ব্যবহার করত, যা পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির প্রমাণ। সিন্ধু নদী ও তার শাখা নদীগুলোতে বাণিজ্যের জন্য নৌকা ব্যবহার করা হতো।
স্থাপত্য ও শিল্প
সিন্ধু সভ্যতায় প্রচুর পরিমাণে সিলমোহর পাওয়া গেছে। সিলমোহরগুলোতে পশুপাখি, দেবতা, এবং দৈনন্দিন জীবনের চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। এগুলো সম্ভবত বাণিজ্যিক বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এগুলো ব্যবহৃত হতো।
কিছু সিলমোহরে “পশুপতি” মূর্তির মতো প্রতীক পাওয়া যায়, যা তাদের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের অংশ হতে পারে।
সিলমোহর ছাড়াও
- নৃত্যরত নারী মূর্তি, পুতুল;
- স্বর্ণ, রূপা, পাথর ও মাটির গয়না;
- ধাতব শিল্প, যেমন তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরি ছুরি, ক্ষুর, কুঠার, কাস্তে;
- পাথরের কাজ,
- টেরাকোটা মূর্তি,
- কুমারের চাক,
- হাতির দাতঁ ও হাড়ের তৈরি চিরুনি ও সুঁচ ইত্যাদি সিন্ধু সভ্যতার উন্নত শিল্পের পরিচয় বহন করে।
ধর্ম ও দর্শন
সিন্ধু সভ্যতার মানুষ প্রকৃতিকে পূজা করত। বৃষ্টি, নদী, গাছপালা এবং পশুপাখি তাদের ধর্মীয় জীবনের অংশ ছিল।
দেবতা, পশু সংবলিত সীলমোহর ঈশ্বর ও প্রাণীদের পূজা করার ইঙ্গিত বহন করে। মাতৃদেবীর মূর্তিকে তারা প্রজননশীলতা এবং উর্বরতার প্রতীকরুপে পূজা করত।
মহেঞ্জোদাড়োর একটি সিলমোহরে শিংযুক্ত মুকুট পরা এবং যোগাসনে বসা একজন দেবতার চিত্র পাওয়া গেছে, যাকে “পশুপতি” বলা হয়। এটি যোগ এবং ধ্যানের প্রাচীন ধারণার সূচনা নির্দেশ করে।
বৃহৎ স্নানাগার পবিত্র স্নানের মাধ্যমে শুদ্ধি অর্জনের ধারণা প্রকাশ করে।
সমাধিস্থলে মৃতদেহের সঙ্গে বিভিন্ন সরঞ্জাম, অলংকার এবং খাদ্য ইঙ্গিত দেয় যে তারা পরকালে বিশ্বাস করত।
এসব ধারণাই পরবর্তিতে প্রাচীন ভারতে দর্শনের মূল ভিত্তি হয়ে উঠে।
তবে তাদের মন্দির ছিল এ রকম কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
ভাষা ও সাহিত্য
সিন্ধু সভ্যতার ভাষা ছোট ছোট চিহ্ন এবং প্রতীক দিয়ে গঠিত ছিল। এ সভ্যতার কিছু লিখিত নিদর্শন পাওয়া গেলেও সেগুলো পুরোপুরি পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।
শেষ পরিণতি
সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের পেছনে একক কোনো কারণ ছিল না। গবেষকদের ধারণা সিন্ধু নদের গতিপথ পরিবর্তন, বন্যা, খরা, জলবায়ুর পরিবর্তন, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়া, মহামারি ইত্যাদি সমস্যার সমন্বিত ফলাফল সিন্ধু সভ্যতার পতন। তবে সুনির্দিষ্ট কারণ এখনো জানা যায়নি। বিতর্ক চলমান রয়েছে।
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে সিন্ধু সভ্যতাই বর্তমান ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি রচনা করেছিল যা পরবর্তীতে আর্যদের মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়। নগর পরিকল্পনা, পরিমাপনবিদ্যা, ধর্ম ও বিশ্বাস ইত্যাদির কারণে ইতিহাস তাদের কখনই ভুলবে না। এদিকে প্রাচীন মিশরেও প্রায় একই রকম একটি সভ্যতার জন্ম হয়েছিল। যাকে আমরা মিশরীয় সভ্যতা নামে চিনি। মিশরীয় সভ্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দর্শক “মিশরীয় সভ্যতা” অনুচ্ছেদটি পারেন।